ঢাকার ব্যস্ত রাস্তাগুলো এখন যেন এক বিশৃঙ্খল মোড়ের গল্প বলে। এক সময় যে শহরে প্যাডেল রিকশাই ছিল প্রধান স্বল্প দূরত্বের বাহন, সেখানে এখন রাজত্ব করছে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক। সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ীতা এবং চালকদের জন্য লাভজনক হওয়ায় এই যানবাহনের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হলেও তা এক ভয়াবহ নগর সংকটেরও জন্ম দিচ্ছে।
🔋 ব্যাটারিচালিত রিকশার উত্থান
২০১০ সালের পর থেকে ঢাকার রাস্তায় ব্যাটারিচালিত রিকশা দেখা যেতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে এগুলো ছিল মূল সড়ক থেকে দূরে, অলিগলির বাহন। কিন্তু ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে এ যানবাহন ব্যাপক আলোচনায় আসে। একদিকে নিষেধাজ্ঞা, অন্যদিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং জনচাপ—এসবের মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় এর ব্যবহার।
২০২৫ সালের মধ্যে ঢাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশার সংখ্যা ১২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। এ সংখ্যা কতটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, তা রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলো—যেমন মিরপুর ১০, বিজয়নগর, পল্টন, কাকরাইল—এ গেলেই বোঝা যায়।
🚧 যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে
১. ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা
ঢাকার প্রধান সড়কগুলোতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রিকশা চলে নির্বিঘ্নে। ব্যাটারিচালিত রিকশা বড় গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে, নিয়ম মানে না। ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল উপেক্ষা করে অনেকে যানচলাচলে বিপর্যয় ঘটায়।
২. নিরাপত্তার অভাব
স্থানীয়ভাবে তৈরি ব্যাটারি ও মোটরযুক্ত রিকশাগুলোর ব্রেকিং সিস্টেম দুর্বল। চালকদের নেই কোনো প্রশিক্ষণ বা লাইসেন্স। দুর্ঘটনার পর এসব রিকশার চালকদের শনাক্ত করাও প্রায় অসম্ভব, কারণ তাদের কোনো নিবন্ধন নেই।
৩. অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা
সিএনজিচালিত অটোরিকশার একটি নিবন্ধিত গাড়ি যেখানে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূল্য পায়, সেখানে মাত্র ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা খরচে ব্যাটারিচালিত রিকশা বানিয়ে দিনপ্রতি ৩০০–৫০০ টাকা আয় করছে মালিকরা। এতে নিয়ন্ত্রিত পরিবহন খাত হুমকির মুখে পড়ছে।
৪. আইন বাস্তবায়নে গাফিলতি
হাইকোর্ট ২০২৪ সালের ১৯ নভেম্বর এসব রিকশার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপের মুখে আইনের প্রয়োগ দুর্বল হয়ে পড়ে।
✅ পক্ষের যুক্তি: কেন এই যান দরকার?
১. সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য – প্যাডেল চালানো কষ্টকর, ব্যাটারি রিকশায় কম খাটুনি দিয়ে বেশি উপার্জন সম্ভব।
২. যাত্রীর চাহিদা – বাস সেবা অপ্রতুল ও হয়রানিমূলক হওয়ায় যাত্রীরা স্বল্প দূরত্বে ব্যাটারিচালিত রিকশাকেই বেছে নিচ্ছেন।
৩. ব্যবসায়িক সম্ভাবনা – চার্জিং স্টেশন ও রিকশা গ্যারেজের মাধ্যমে একটি নতুন ক্ষুদ্র ব্যবসা খাত গড়ে উঠেছে।
🔍 কারা দায়ী?
-
নগর কর্তৃপক্ষ: ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাতে নেই কোনো হালনাগাদ ডেটাবেস।
-
ট্রাফিক বিভাগ: সড়কে ফাঁদ বসালেও বাস্তবিক প্রয়োগ ব্যর্থ হচ্ছে।
-
বিদ্যুৎ সংস্থাগুলো: চার্জিং স্টেশনগুলো বৈধতা দিচ্ছে, কিন্তু পরিবহন নীতির সঙ্গে সমন্বয়হীন।
-
নীতিনির্ধারকরা: ২০২১ সালের নীতিমালার খসড়া থাকলেও তা এখনো অনুমোদন পায়নি।
🛣️ সমাধানের পথ
🔹 নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং
সব ব্যাটারিচালিত রিকশা ও চালককে সিটি করপোরেশনের আওতায় এনে নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।
🔹 নিরাপদ ডিজাইন ও মানদণ্ড নির্ধারণ
শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএ মিলে স্থানীয়ভাবে নিরাপদ ডিজাইনের রিকশা তৈরি নিশ্চিত করতে পারে।
🔹 ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণ
কোন সড়কে কোন ধরণের যান চলতে পারবে, তার একটি মানচিত্র তৈরি করে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
🔹 বাস সেবার আধুনিকায়ন
সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও নারী-সহায়ক বাস সেবা চালু করলেই রিকশার চাপ কমানো সম্ভব।
🧠 উপসংহার
রিকশা একদিন ছিল ঢাকার প্রাণ, এখন হয়ে উঠেছে এক বিশৃঙ্খলার প্রতীক। তবে এটিকে দোষ দিয়ে পুরো দায় এড়ানো যাবে না। বরং ব্যাটারিচালিত রিকশার প্রসঙ্গটি নগর ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা, পরিবহন খাতের অনিয়ম ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিচ্ছবি।
সমাধান অসম্ভব নয়—কিন্তু দরকার সদিচ্ছা, সমন্বিত নীতি এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনা।


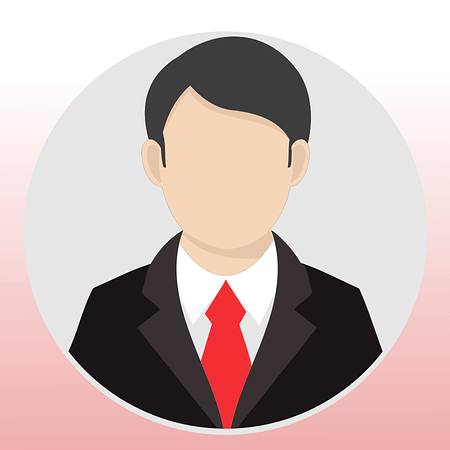















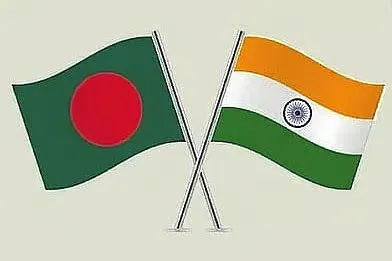



























✍️ মন্তব্য লিখুন